জ্বালানিবিদ্যার মৌলিক তাৎপর্য
প্রকাশিত:
২০ জানুয়ারী ২০২৫ ০৫:৩৬
আপডেট:
৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ ১৫:৫০
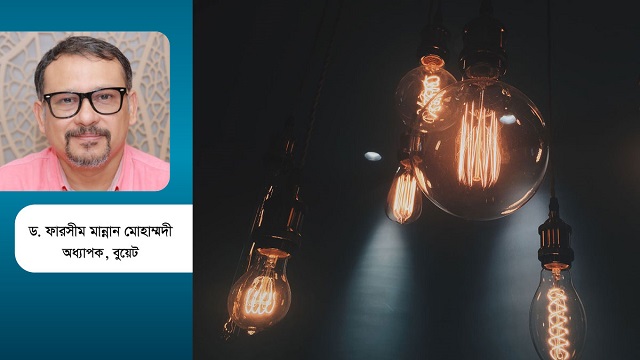
জ্বালানি ব্যবসায়ে আমরা সবসময়েই জ্বালানির অর্থমূল্য বিচার করে থাকি। কয়লার মূল্য টনপ্রতি কত টাকা পড়ছে, ব্রেন্ট তেলের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে গত সপ্তাহের চেয়ে এই সপ্তাহে বাড়ল কিনা, এলএনজি’র দাম ওমানের বাজারে কত হলো ইত্যাদি।
বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও আমরা শক্তি-উৎস বিচারে কিলোওয়াট-ঘণ্টা প্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদনে কোন উৎসের জন্য কত টাকা লাগছে সেটা বিচার করি। অর্থনৈতিক এবং অর্থমূল্যের বিচারে, ইকোনমিক, ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং এবং ফোরকাস্টের কাজে এই হিসাব অবশ্য-প্রয়োজনীয়।
ফিস্কাল প্ল্যানিং বা বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ইউনিট প্রতি উৎপাদন মূল্য অথবা আমদানি মূল্য আমাদের উল্লেখ করতে হয় এবং বাজেট বিশ্লেষণের কাজে বিভিন্ন গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের সংবাদ-সম্মেলনেও আমরা বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি মূল্য নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুনি এবং দেখি।
তবে জ্বালানিবিদ্যায় আরও একটি প্যারামিটার আছে যার বৈজ্ঞানিক মূল্য কম নয়। এবং অনেক মৌলিক বিশ্লেষণের কাজে আলোচনার পেছনে কিন্তু এই প্যারামিটারটি রয়েই যায়। এটি হলো শক্তি-ঘনত্ব বা এনার্জি ডেনসিটি। শক্তি ও জ্বালানি গবেষণার অনেক মৌলিক বিষয় বুঝতে হলে এই শক্তি ঘনত্বের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হয়।
এটি যত না অর্থনৈতিক টার্ম, তারও চেয়ে বেশি বৈজ্ঞানিক শব্দ এবং প্রকৌশল পরিভাষা। যেজন্য সচরাচর আমরা এই শব্দটি শুনি না, এর অর্থও বুঝি না। আমাদের কালেকটিভ কনশাসনেস বা সামগ্রিক চেতনা যেহেতু নির্মিত হয় জনপ্রিয় সংবাদ সম্মেলন থেকে রসদ জুগিয়ে, তাই বৈজ্ঞানিক গুরুত্বপূর্ণ টার্ম বাদ পড়ে যায় বোধের সীমানা থেকে।
এর ফল খুব সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না, কেননা সাধারণ মৌখিক আলাপচারিতায় অর্থনৈতিক টার্ম যতটা আবেদন সৃষ্টি করে, বৈজ্ঞানিক টার্ম ততটা করে না। জ্বালানিবিদ্যার আলাপচারিতা সর্বদাই টাকাকড়ির আলোচনায় ঘোরাফেরা করার ফলে জ্বালানিখাতের গবেষণাজনিত অসুবিধাগুলো বা শক্তি-উৎসের টেকনোফিজিবিলিটি কিংবা সরল প্রকৌশলগত হিসাব আমলে নেওয়া হয় না।
অনেক সময় বিশেষজ্ঞরাও ভুলে যান, জনপ্রিয় টার্মের ভিড়ে প্রকৃত প্যারামিটার হারিয়ে যায়। এটাকে আপনি বিজ্ঞান চেতনার কলোনিয়াল হ্যাঙওভারও বলতে পারেন, তবে এর মূল কারণ হলো মৌলিক গবেষণা যেহেতু আমাদের দেশে হয় না এবং যেহেতু নীতিগত কিংবা সিদ্ধান্তের জায়গাগুলো নির্ধারিত হয় দাতাদের টেবিলে বা আমলাদের বৈঠকে এবং কখনো কখনো সংবাদ সম্মেলনে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে।
যা বলছিলাম, শক্তি ঘনত্বের কথা একটা খুব জরুরি প্যারামিটার। শক্তি-ঘনত্বের তুলনা করলেই বোঝা যায়, ফসিল ফুয়েল বা জীবাশ্ম-জ্বালানি কেন বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। জীবাশ্ম-জ্বালানির পুরোটাই হাইড্রোকার্বন-উদ্ভূত কেননা তেল-গ্যাস-কয়লার সবটাই কার্বন-ভিত্তিক জৈবযৌগ। এসব জৈবযৌগের দহনের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়।
যদিও তাদের দহনে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়, তবু কিন্তু আমরা গণহারে এদের ত্যাগ করতে পারছি না। কেন পারছি না, সেটার একটি প্রধান কারণ শক্তি-ঘনত্ব। প্রথমত, এটা স্পষ্ট যে জীবাশ্ম জ্বালানির শক্তি-ঘনত্ব অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, হাইড্রোকার্বনের আরেকটি সুবিধা হলো এর সহজে বহনযোগ্যতা ও স্থানান্তর যোগ্যতা।
খুব সহজেই গ্যাস বা তেলকে আমরা আন্তঃমহাদেশীয় পাইপলাইন বা সমুদ্রগামী বিশাল ট্যাংকারের সাহায্যে স্থানান্তর করতে পারি। পুরো ব্যাপারটির নিয়ন্ত্রণও খুব ভালো-লস কম, দক্ষতা বেশি, প্রবাহ সুনিয়ন্ত্রিত, নিরাপত্তা পর্যাপ্ত।
একক ওজনে শক্তির মাপ অনুযায়ী শুকনো কাঠ খুব কম শক্তি দেয় (১৬ গিগাজুল/টন), এরপর আছে প্রায় দ্বিগুণ ঘনত্বের বিটুমিন কয়লা (২৪-৩০ গিগাজুল/টন)। এদের সাথে যদি কেরোসিন ও ডিজেলের (৪৬ গিগাজুল/টন) তুলনা করা হয় তবে দেখা যাবে শেষোক্ত উৎসের ঘনত্ব কাঠের অন্তত তিনগুণ বেশি।
আয়তন অনুপাতে শক্তি ঘনত্ব যদি তুলনা করা যায় তবে দেখা যাবে—কাঠ (১০ গিগাজুল/ঘনমিটার), কয়লা (২৬ গিগাজুল/ঘনমিটার), কেরোসিন (৩৮ গিগাজুল/ঘনমিটার), প্রাকৃতিক গ্যাস (০.০৩৫ গিগাজুল/ঘনমিটার)। দেখা যাচ্ছে, একক আয়তনে কেরোসিন কাঠের প্রায় ৪ গুণ শক্তিধর। তবে গ্যাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্যাসীয় দশার কারণে এর ঘনত্ব খুবই কম। [ভাক্লাভ স্মিলের সূত্রমতে]
দুটো ব্যাপার লক্ষণীয়—ওজন হিসাবে ঘনত্ব এবং একক আয়তন হিসাবে ঘনত্ব। ওজন হিসাবে শক্তি-ঘনত্বের তাৎপর্য হলো একক ওজনের জ্বালানি কী পরিমাণ শক্তি দিচ্ছে। যে উৎসের শক্তি-ঘনত্ব বেশি, তার সামান্য একটু নিলেই কাজ হয়ে যাবে, যার ঘনত্ব কম তার বেশি আয়তনের নিতে হবে। জাহাজ বা প্লেন চালনায় ওজনের ব্যাপারটা খুব দরকারি।
আটলান্টিক পাড়ি দিতে জাহাজে যদি কাঠ দিয়ে জ্বালানি সরবরাহের কাজ করতে হতো, তবে বিশাল ওজনের কাঠ বহন করতে হতো। কিন্তু ডিজেল দিয়ে চালালে ওজনের একটা বড় অংশ সাশ্রয় হয়, আয়তনও কম লাগে (আড়াইগুণ কম!)। তুলনায় যদি ব্যাটারির কথা ভাবেন, তাহলে সহজেই বোঝা যাবে কেন ব্যাটারি দিয়ে প্লেন চালানো যাচ্ছে না।
কারণ, দূর-পাল্লার প্লেন উড়তে যে পরিমাণ শক্তি প্রয়োজন হবে সেটুকু দিতে যতটুকু ব্যাটারি লাগবে তার ফলে যাত্রীদের আর বসার জায়গা থাকবে না! এজন্য ইলেকট্রিক প্লেনের কথা ভাবা সুদূর পরাহত, যদি না অবশ্য খুব আধুনিক যুগান্তকারী কোনো আবিষ্কার হচ্ছে যা ব্যাটারির শক্তি-ঘনত্বকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেবে, সেইসাথে তার ওজনকে ততটুকু কমিয়ে দেবে।
আবার একক আয়তনের শক্তি-ঘনত্বের ব্যাপারটাও জরুরি। প্লেনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে, ওজন যত কম হয় তত ভালো। ফলে প্লেনের জন্য এভিয়েশন-গ্রেড কেরোসিন বেশি পছন্দনীয়, কেননা প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনায় তা অনেক কম আয়তনের কিন্তু উচ্চ শক্তি-ঘনত্বের (১০০০ গুণ!) হয়ে থাকে।
আবার একই শক্তি দিতে কয়লার তুলনায় গ্যাস ৭০০ গুণের বেশি জায়গা নেবে। কিন্তু কয়লার তুলনায় গ্যাস অনেক অনেক পরিচ্ছন্ন একটি জ্বালানি। আবার দূরের কূপ থেকে শিল্পাঞ্চলে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস টেনে আনা অনেক সহজ; তুলনায় কয়লা আনতে হতো ট্রাক বা ট্রেনে করে এবং পুরো যাত্রাপথ কয়লার দূষণে দূষিত হয়ে যেত। তাই শিল্প-কারখানায় জ্বালানি হিসেবে গ্যাস অনেক বেশি কাঙ্ক্ষিত।
প্রতি বর্গমিটারে জ্বালানি-উৎসের ঘনত্ব আরেকটি প্যারামিটার যা চিন্তার উদ্রেক করে। বর্গমিটারে শক্তি-ঘনত্বের বিচারে জীবাশ্ম-জ্বালানির অগ্রগণ্যতা অনস্বীকার্য, জীবাশ্ম জ্বালানি (৫০০ – ১০,০০০ ওয়াট / বর্গমিটার), পরমাণু বিদ্যুৎ (৫০০ – ১,০০০ ওয়াট / বর্গমিটার), সোলার (৫ – ২০ ওয়াট / বর্গমিটার), জলবিদ্যুৎ (৫ – ৫০ ওয়াট / বর্গমিটার), বায়ু-বিদ্যুৎ (১ – ২ ওয়াট / বর্গমিটার), কাঠ ও অন্যান্য বায়োগ্যাস (<১ ওয়াট / বর্গমিটার) [বিল গেইটসের সূত্রমতে]।
সামান্য ক্ষেত্রফল থেকে সুপ্রচুর ওয়াট কেবল ফসিলই দিতে পারে। এইদিক বিবেচনায় ভূতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত এই উপহারটি অসীম সম্ভাবনার। কোনো সন্দেহ নেই কেন ফসিল ফুয়েল নিয়ে দুনিয়া-জোড়া এই মাতামাতি। সেই তুলনায় জৈব উৎস অনেক ম্রিয়মাণ।
ঐতিহাসিক কালে কেন সভ্যতা শ্লথগতির ছিল তা এই হিসাব দেখলেই বোঝা যায়। সোলারের ক্ষমতা আরও একটুখানি ভালো, তবে এক বর্গমিটারে তার বৈদ্যুতিক দক্ষতা কম বিধায় যে শক্তিটুকু পাওয়া যায় তা বিদ্যুতে রূপান্তর হয় কম। তদুপরি গড় হিসাব নিলে এটা আরও কমে যায়, কারণ দিনের অর্ধেক সময়েই কিন্তু সূর্য থাকে না, উপরন্তু মেঘের আনাগোনা একটা বড় অনবচ্ছিন্নতার কারণ।
নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে অনবচ্ছিন্নতা বা ইন্টারমিটেন্সি একটি বড় সমস্যা। এটি বৈদ্যুতিক গ্রিডের সুস্থিতির জন্য বড় সমস্যা করবে, যখন নবায়নযোগ্য উৎস থেকে অনেক বেশি পরিমাণে বিদ্যুৎ আসা শুরু করবে। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে জ্বালানির মৌলিক সমস্যা নিরূপণে তাই শক্তি-ঘনত্বের মতো প্যারামিটার আমাদের বোধকে সাহায্য করবে। শক্তি-ঘনত্বের এই প্যারামিটার দেখে জ্বালানি খাত নিয়ে নতুনভাবে ভাবা দরকার।
ড. ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী ।। পরিচালক, জ্বালানি ও টেকসই গবেষণা ইন্সটিটিউট; অধ্যাপক, তড়িৎকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়


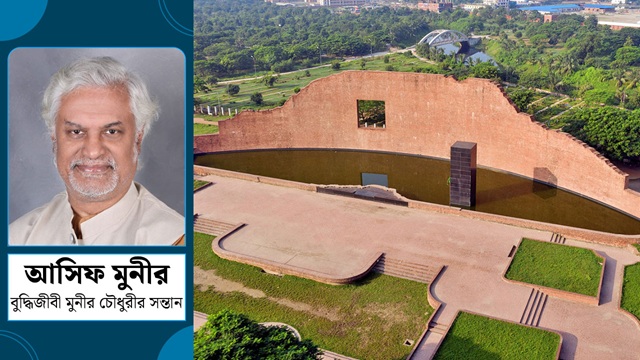

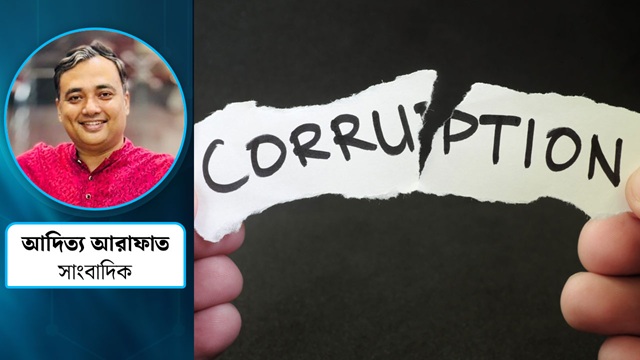



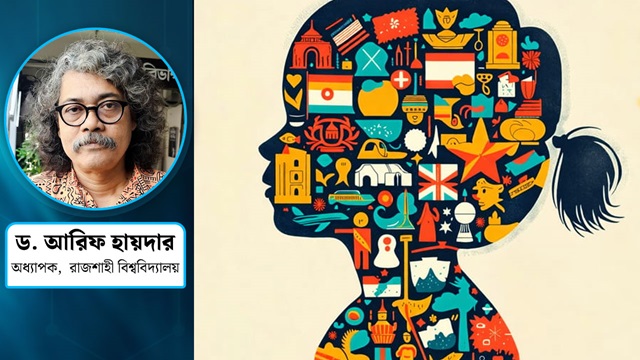
আপনার মূল্যবান মতামত দিন: