উলবাকিয়া কি ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সক্ষম?
প্রকাশিত:
১০ মে ২০২৫ ০৭:৫৭
আপডেট:
২৭ জানুয়ারী ২০২৬ ১৯:৪২
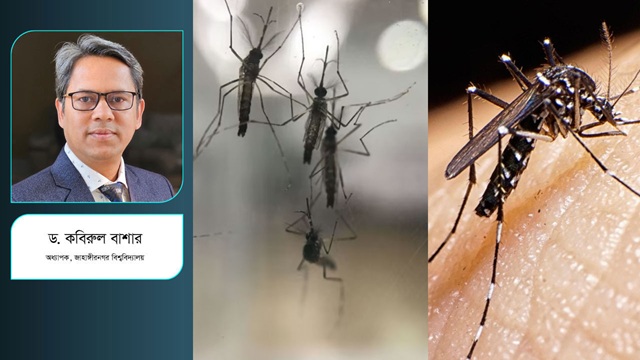
ডেঙ্গু (Dengue) একটি মারাত্মক মশাবাহিত রোগ যা বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর লক্ষাধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটায়। বাংলাদেশে, বিশেষ করে ঢাকা শহরে, ডেঙ্গুর প্রকোপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে উলবাকিয়া ব্যাকটেরিয়া (Wolbachia Bacteria) ব্যবহার করে মশা দমনের পদ্ধতি একটি সম্ভাবনাময় সমাধান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বিভিন্ন দেশে। এই প্রযুক্তি বাংলাদেশে আনার জন্য নানা ধরনের কার্যক্রম ও প্রচারণা চলছে।
নতুন একটি প্রযুক্তি বাংলাদেশে আনার পূর্বে এর সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান এবং এটি কতটা সফলতা এনে দেবে তা নিয়ে অভিজ্ঞ কীটতত্ত্ববিদদের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন। দীর্ঘ ২৬ বছর ধরে মশার আদ্যোপান্ত নিয়ে দেশে-বিদেশে গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে উলবাকিয়া প্রযুক্তির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, ঢাকা শহরে এর কার্যকারিতা, সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ এবং বাস্তবায়নের খরচ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি।
উলবাকিয়া ব্যাকটেরিয়া: বৈজ্ঞানিক ভিত্তি
উলবাকিয়া (Wolbachia) হলো একটি প্রাকৃতিক ব্যাকটেরিয়া যা পৃথিবীর ৬০ শতাংশ পোকামাকড়ের দেহে বসবাস করে। এটি মানুষের জন্য ক্ষতিকর নয়, তবে এটি মশার প্রজনন ক্ষমতা এবং ডেঙ্গু ভাইরাস বহন করা ক্ষমতা নষ্ট করতে সক্ষম। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, উলবাকিয়া-আক্রান্ত এডিস ইজিপ্টাই মশা ডেঙ্গু ভাইরাসের প্রতিলিপি তৈরি করতে অক্ষম। এই ব্যাকটেরিয়া মশার ডিমের বিকাশেও বাধা সৃষ্টি করে, ফলে মশার সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।
উলবাকিয়া (Wolbachia) ব্যাকটেরিয়া পুরুষ মশার পুরুষত্ব নষ্ট করে বন্ধ্যা করে দেয়। এই ব্যাকটেরিয়া শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির এডিস মশার সংখ্যা কমাবে অন্য প্রজাতির মশার ক্ষেত্রে এটি কোনো ভূমিকা রাখবে না। উলবাকিয়া বহনকারী মশা ছেড়ে দেওয়া বন্ধ করে দিলে সেই এলাকাতে ধীরে ধীরে মশার সংখ্যা আবার স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসবে।
প্রযুক্তির প্রয়োগ পদ্ধতি
উলবাকিয়া প্রযুক্তির (Wolbachia Technology) প্রয়োগ শুরু হয় ল্যাবরেটরিতে এডিস মশার কলোনি তৈরি করে, যেখানে বিশেষ পদ্ধতিতে মশার ডিমে উলবাকিয়া ব্যাকটেরিয়া প্রবেশ করানো হয়। ডিম ফুটে বের হওয়া মশাগুলো থেকে শুধুমাত্র পুরুষ মশাগুলো বাছাই করে ডেঙ্গুপ্রবণ এলাকায় নিয়মিতভাবে মুক্ত করা হয়। প্রকৃতিতে থাকা স্ত্রী মশার সাথে যখন এই উলবাকিয়া-আক্রান্ত বন্ধ্যা পুরুষ মশা মিলিত হয়, তখন সৃষ্ট ডিম থেকে মশার লার্ভা তৈরি হয় না, ফলে মশার সংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।
একইসাথে, উলবাকিয়া-আক্রান্ত স্ত্রী মশাগুলো ডেঙ্গু ভাইরাস বহন ও সংক্রমণ করতে অক্ষম হয়, যা ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। এই প্রক্রিয়ার সাফল্য নিশ্চিত করতে প্রতি সপ্তাহে বিপুল সংখ্যক উলবাকিয়া-আক্রান্ত পুরুষ মশা মুক্ত করতে হয় এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণের জন্য এলাকাভিত্তিক মশার ঘনত্ব ও ডেঙ্গু সংক্রমণের হার নিয়মিত মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।
উলবাকিয়া পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কিনা?
এটি যেহেতু প্রকৃতিতে থাকা ব্যাকটেরিয়া এবং প্রকৃতিতে সাধারণভাবেই এটি পাওয়া যায় তাই এই ব্যাকটেরিয়াটি দ্বারা পরিবেশ প্রকৃতির কোনো ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। তারপরও এটি নিয়ে বিস্তর গবেষণা প্রয়োজন। মানব স্বাস্থ্যের জন্য এটি ক্ষতিকর কিনা তারও কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। এই বিষয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।
ঢাকা শহরে উলবাকিয়া প্রযুক্তির কার্যকারিতা
ঢাকা শহরে উলবাকিয়া প্রযুক্তির সাফল্য নির্ভর করবে শহরের অনন্য চ্যালেঞ্জগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এর বাস্তবায়ন কৌশলের ওপর - উচ্চ জনঘনত্ব, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং ব্যাপক মশার প্রজননস্থল (যেমন নির্মাণাধীন স্থানের পাত্রে জমে থাকা পানি, বহুতল ভবনের পার্কিংয়ে জমা পানি, ছোট বড় অসংখ্য পাত্র) এই প্রযুক্তির কার্যকারিতাকে জটিল করে তোলে।
তবে, ইন্দোনেশিয়ার ইয়োগিয়াকার্তার মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে এই পদ্ধতি ৭৭ শতাংশ ডেঙ্গু হ্রাসের সাফল্য দেখিয়েছে বলে কোম্পানিগুলো জানাচ্ছে। এই প্রযুক্তির মূল চাবিকাঠি হলো চিহ্নিত জায়গায় প্রচুর পরিমাণে মশা ছেড়ে দেওয়া। ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ নগরীতে উলবাকিয়া প্রযুক্তি কার্যকর করতে প্রকৃতিতে বিদ্যমান এডিস মশার চেয়ে ৫-১০ গুণ বেশি উলবাকিয়া-আক্রান্ত পুরুষ মশা নিয়মিত ছাড়তে হবে।
বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, প্রতি হেক্টরে সাপ্তাহিক ১০০-১৫০টি মশা ছাড়লে কার্যকর ফল পাওয়া যায়, যা ঢাকার ৩০০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় সাপ্তাহিক ৩০-৪৫ লাখ মশা ছাড়ার সমতুল্য। প্রথম ৬ মাস উচ্চমাত্রায় (সপ্তাহে ১-২ বার) এবং পরবর্তীতে রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ে (সপ্তাহে ১ বার) মশা ছাড়তে হবে, বিশেষ করে ঢাকার দূষিত পরিবেশে মশার আয়ু কমে যাওয়ায় এই সংখ্যা আরও বাড়ানো প্রয়োজন।
তবে এই অনুপাত স্থানীয় মশার ঘনত্ব, তাপমাত্রা ও প্রজনন হার বিবেচনায় সামঞ্জস্য করতে হবে, যার জন্য পাইলটিং এবং নিয়মিত মনিটরিং আবশ্যক। প্রাথমিকভাবে মিরপুর বা গুলশানের মতো সু-সংজ্ঞায়িত এলাকায় পাইলটিং এবং পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণই হতে পারে বাস্তবসম্মত পথ, যদিও দীর্ঘমেয়াদি সাফল্যের জন্য স্থানীয় পরিবেশে উলবাকিয়া-মশার অভিযোজন ক্ষমতা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে টেকসই অর্থায়ন নিশ্চিত করা অপরিহার্য।
সমন্বিত পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা
উলবাকিয়া প্রযুক্তির টেকসই সাফল্যের জন্য একটি সমন্বিত মশা ব্যবস্থাপনা কৌশল অপরিহার্য, যার মধ্যে প্রথমত নাগরিক অংশগ্রহণে মশার প্রজননস্থল ধ্বংস (বাড়ির আশেপাশের পানি জমে থাকা পাত্র, নির্মাণাধীন স্থান, ফেলে রাখা টায়ার ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার),
দ্বিতীয়ত লার্ভিসাইড (বিশেষ করে বিটিআই বা স্পিনোসাড ভিত্তিক পরিবেশবান্ধব লার্ভিসাইডের ব্যবহার),
তৃতীয়ত কমিউনিটি ভিত্তিক সচেতনতা কর্মসূচি (স্কুল ও স্থানীয় ক্লাবগুলো সম্পৃক্ত করে),
চতুর্থত স্মার্ট নজরদারি ব্যবস্থা (জিআইএস ম্যাপিং ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে মশার ঘনত্ব রিয়েল-টাইমে ট্র্যাক করা)
এবং পঞ্চমত স্থানীয় সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টা (সিটি কর্পোরেশন, স্বাস্থ্য বিভাগ ও পরিবেশ অধিদপ্তরের যৌথ কার্যক্রম) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে—এই বহুমুখী পদ্ধতি ছাড়া শুধুমাত্র উলবাকিয়া প্রযুক্তি ঢাকার মতো অতি-ঘনবসতিপূর্ণ ও অপরিকল্পিত নগরীতে কার্যকর হওয়া অসম্ভব, যেমনটি ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার অভাবেই প্রাথমিকভাবে উলবাকিয়া প্রকল্পের সীমিত সাফল্য দেখা গিয়েছিল।
ঢাকা শহরে উলবাকিয়া প্রযুক্তি বাস্তবায়নের গভীর চ্যালেঞ্জসমূহ
ঢাকা শহরের মতো অতি ঘনবসতিপূর্ণ, দূষিত ও অপরিকল্পিত নগরীতে উলবাকিয়া প্রযুক্তি বাস্তবায়নে নানাবিধ জটিল চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যা এই প্রযুক্তির কার্যকারিতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে।
প্রথমত, পরিবেশগত প্রতিকূলতা একটি বড় বাধা হিসেবে কাজ করে। ঢাকার উচ্চ তাপমাত্রা, বায়ু দূষণ এবং ভারী ধাতুর উপস্থিতি ল্যাবরেটরিতে উৎপাদিত উলবাকিয়া-আক্রান্ত মশাগুলোর বেঁচে থাকার সক্ষমতা কমিয়ে দেয়। গবেষণা বলছে, দূষিত পরিবেশে এই মশাগুলোর জীবনকাল প্রায় ৩০ শতাংশ কমে যায়, যা তাদের প্রজনন ক্ষমতাকে ব্যাহত করে।
দ্বিতীয়ত, মশার অত্যধিক ঘনত্ব এবং বিস্তৃতি একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। ঢাকা শহরে প্রতি বর্গকিলোমিটারে দুই লাখের বেশি মশার বসবাস, যা বিশ্বের অন্যতম উচ্চ হার। এত ঘনত্বের মধ্যে সীমিত সংখ্যক উলবাকিয়া-আক্রান্ত মশা ছেড়ে দেওয়া প্রকৃতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে ব্যর্থ হতে পারে।
তৃতীয়ত, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং মশার প্রজননস্থলের ব্যাপকতা এই প্রযুক্তির কার্যকারিতা হ্রাস করে। ঢাকার ৬০ শতাংশ এডিস মশার প্রজননস্থল হলো বাড়ির ছাদে, নির্মাণাধীন স্থান, বহুতল ভবনের বেসমেন্টে জমা পানি, বিভিন্ন ধরনের ছোট-বড় পাত্রে জমে থাকা পানি, যা নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন।
চতুর্থত, প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এই প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তোলে। ঢাকার স্থানীয় এডিস মশার জিনগত বৈচিত্র্য ল্যাবরেটরিতে তৈরি পুরুষ উলবাকিয়া-আক্রান্ত মশার সাথে সঙ্গমে অনিচ্ছা সৃষ্টি করতে পারে, যা মশার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের হারকে কমিয়ে দেয়।
পঞ্চমত, সামাজিক ও প্রশাসনিক বাধা যেমন স্থানীয় জনগণের অসচেতনতা, সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের অভাব এই প্রযুক্তির টেকসই বাস্তবায়নে বড় ধরনের অন্তরায় সৃষ্টি করে।
অবশেষে, মনিটরিং এবং মূল্যায়নের অভাব এই প্রযুক্তির সাফল্যকে অনিশ্চিত করে তোলে। ঢাকার মতো বিশাল ও জটিল নগরীতে মশার ঘনত্ব, ডেঙ্গুর হার এবং উলবাকিয়ার প্রভাব সঠিকভাবে ট্র্যাক করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এছাড়া, ডেঙ্গু ভাইরাসের মিউটেশন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এই প্রযুক্তির দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতাকে আরও অনিশ্চিত করে তোলে।
সুতরাং, ঢাকার মতো মহানগরীতে উলবাকিয়া প্রযুক্তি বাস্তবায়নে একটি সমন্বিত, বৈজ্ঞানিক এবং স্থানীয়ভাবে অভিযোজিত কৌশল প্রয়োজন, যাতে উপরের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে টেকসই ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়।
সমস্যা এবং উদ্বেগ
এই মশাটি যেসব দেশে ছাড়া হয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগ ছিল দ্বীপ অঞ্চল। দ্বীপ অঞ্চলে চারদিকে পানি থাকার কারণে মশাগুলো যেখানে ছাড়া হয় সেই এলাকাতেই থাকে। ঢাকার মতো মেগা সিটি, যেখানে আলাদা প্রাকৃতিক বাউন্ডারি নেই সেখানে এ পদ্ধতি কতটা কার্যকরী হবে সেটি নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।
এছাড়াও ল্যাবরেটরিতে তৈরি করা উলবাকিয়া বহনকারী পুরুষ মশাকে যখন প্রকৃতিতে ছেড়ে দেওয়া হবে তখন ওই প্রকৃতিতে টিকে থাকা হবে তার জন্য প্রথম চ্যালেঞ্জ। ল্যাবরেটরি পরিবেশ এবং বাইরের পরিবেশ এক নয়। প্রকৃতির তাপমাত্রা, বাতাসের বেগ, দূষণ এই সবগুলোর বিরুদ্ধে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে বেঁচে থাকা হবে তার জন্য কঠিন।
প্রকৃতির প্রতিকূলতার মধ্যে খাপ খাইয়ে যারা বেঁচে যাবে তারা স্ত্রী মশার সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাবে। প্রকৃতিতে থাকা পুরুষ মশার সাথে এবার শুরু হবে তাদের যৌন প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রকৃতিতে থাকা পুরুষ মশার জয়ী হওয়ার সম্ভাবনাটাই বেশি থাকবে। কারণ ওই প্রকৃতি এবং পরিবেশে এই মশাটি বেড়ে উঠেছে এবং তার সঙ্গে বড় হওয়া স্ত্রী মশাটির সখ্যতা রয়েছে। প্রকৃতিতে থাকা স্ত্রী মশারও পছন্দের বিষয় থাকবে। প্রকৃতিতে থাকা স্ত্রী মশা কাকে তার যৌনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিবে সেটি তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ এবং যৌন প্রতিযোগিতার ওপর নির্ভর করবে।
ডেঙ্গু ভাইরাস, আরএনএ ভাইরাস হওয়ার কারণে এর উচ্চ মিউটেশন ক্ষমতা রয়েছে এবং মিউটেশনের হার ডিএনএ জিনোমের মিউটেশন হারের চেয়ে ১০০ গুণ বেশি। উলবাকিয়া ডেঙ্গুভাইরাসের মিউটেশন ঘটিয়ে কোন নতুন সেরো টাইপ সৃষ্টি করবে কিনা সেটিও গবেষণার বিষয়।
যদি এই মশাটি বিদেশ থেকে আমদানি করে ছাড়া হয় তাহলে কত সংখ্যক আনা হলো বা ছাড়া হলো সেটি গণনা করা কঠিন। বাংলাদেশে যেহেতু আমরা বিভিন্ন কাজে দুর্নীতির কথা শুনি তাই এখানে মশা ছাড়ার সংখ্যা এবং এর ব্যয় নিয়ে একটি বিস্তর গরমিল হতে পারে।
পৃথিবীতে যেহেতু এই প্রযুক্তি নিয়ে নানান ভাবে আলোচনা হচ্ছে এবং এই প্রযুক্তি উদ্ভাবকেরা চেষ্টা করেছে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটিকে বিক্রি করার। তাই আমাদের দেশ এটির ব্যবহার নিয়ে ভাবতে পারে। তবে তার আগে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে থেকে রাষ্ট্রীয় অনুমোদন প্রয়োজন।
এছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েরও অনুমোদন অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে এই প্রযুক্তিটি ব্যবহার ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে কতটা ভূমিকা রাখবে সেই বিষয়ে গবেষকদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিদেশ থেকে মশা আমদানি না করে বাংলাদেশেই এই প্রযুক্তিতে মশা তৈরি করে পরীক্ষামূলকভাবে ছোট কয়েকটি এলাকাতে ছেড়ে তার ফলাফল পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। ছোট এলাকাগুলোতে এটি সফল হলে দেশব্যাপী এই কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে।
ড. কবিরুল বাশার ।। অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
[email protected]


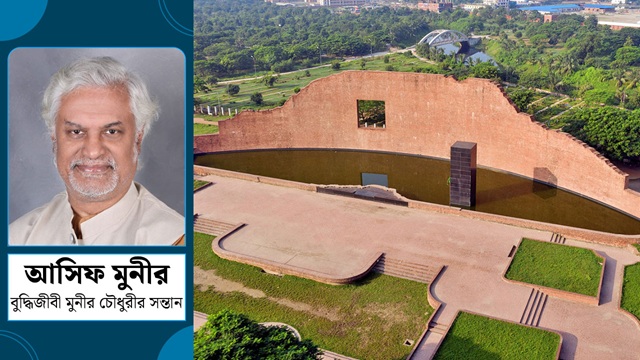

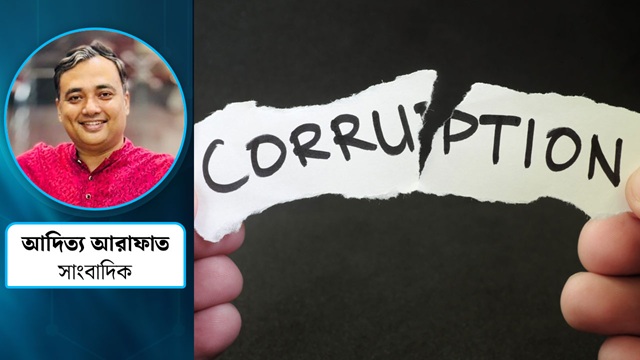



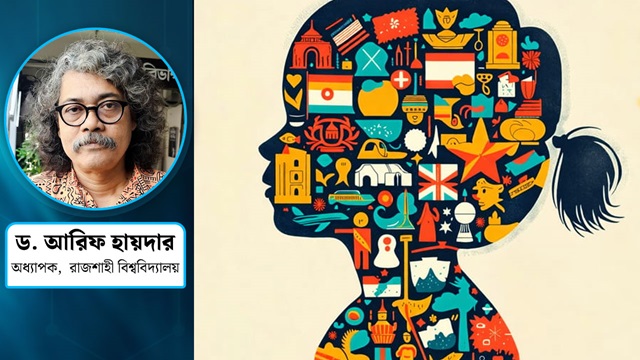
আপনার মূল্যবান মতামত দিন: