ভূমিকম্প, সুনামি : দায়, দৃষ্টি ও প্রস্তুতি
প্রকাশিত:
৩১ জুলাই ২০২৫ ০৬:২৬
আপডেট:
২৭ জানুয়ারী ২০২৬ ১৯:১৫

জাপানের রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন এনএইচকের উপস্থাপককে বারবার বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘দয়া করে দ্রুত সরে যান। সম্ভব হলে, উঁচু জায়গায় যান এবং উপকূল থেকে দূরে থাকুন’। রাশিয়ার দূর প্রাচ্যের পেত্রোপাভলোভস্ক-কামচাতস্কি উপকূলে ৮.৮ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর প্রায় চার মিটার উচ্চতার সুনামির প্রথম ঢেউ উত্তর জাপানের হোক্কাইডোতে আঘাত হেনেছে।
রয়টার্স জানিয়েছে, প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়েছে; অনেক এলাকা থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস জানিয়েছে, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল পেত্রোপাভলোভস্ক-কামচাতস্কি শহর থেকে ১১৯ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্বে এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে এর গভীরতা ছিল ১৯.৩ কিলোমিটার। এর ফলেই জাপানের হোক্কাইডো উপকূলে সুনামির প্রথম ঢেউ আঘাত হানে।
ঢেউয়ের উচ্চতা ছিল প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার (১২ ইঞ্চি), যা পৌঁছায় হোক্কাইডোর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বন্দরনগরী নেমুরোতে। ২০১১ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্প ও সুনামির ক্ষতচিহ্ন এখনও বহন করে চলা জাপানের পূর্ব উপকূল জুড়ে আবারও সতর্কতা জারি করে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এই ভূমিকম্প ও সুনামির ঘটনা অনেকটাই ‘মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা’ প্রবাদটির মতোই। ভূমিকম্প ও সুনামির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, যদিও সব ভূমিকম্প সুনামি সৃষ্টি করে না। সাধারণত সমুদ্রের তলে শক্তিশালী ভূমিকম্প হয় যখন টেকটোনিক (Tectonic) প্লেটের উল্লম্ব স্থানচ্যুতি ঘটে, তখন বিশাল পরিমাণ পানি স্থানচ্যুত হয়ে সুনামির সৃষ্টি করে।
বিশেষ করে সাবডাকশন জোনে—যেখানে এক টেকটোনিক প্লেট আরেকটির নিচে ঢুকে যায়—এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০৪ সালের ভারত মহাসাগরের তলদেশে ৯.১ মাত্রার ভূমিকম্পটি ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ সুনামি সৃষ্টি করেছিল।
ইন্দোনেশিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে এই সুনামি দক্ষিণ এশিয়ার বহু দেশে—যেমন ভারত, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডে—ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং প্রায় ২,৩০,০০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ২০১১ সালের জাপানের তোহোকু অঞ্চলের ৯.০ মাত্রার ভূমিকম্প।
এটি সমুদ্রতলে ব্যাপক স্থানচ্যুতি ঘটায় এবং এর ফলে সৃষ্ট সুনামি প্রায় ৪০ মিটার উচ্চতায় পৌঁছে। এই সুনামি উপকূলে বিধ্বংসী ঢেউ আছড়ে ফেলে এবং ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী। এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে সুনামির উৎস সাধারণত সমুদ্রতলে সংঘটিত শক্তিশালী ভূমিকম্প এবং উল্লম্ব স্থানচ্যুতি এতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
তবে ভূমিকম্প ও সুনামি নিয়ে আমাদের সমাজে কিছু ভুল ধারণা রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে এসব দুর্যোগের মাত্রা ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাস্তবতা কিছুটা আলাদা। ভূমিকম্পের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই, কারণ ভূমিকম্প মূলত পৃথিবীর অভ্যন্তরে টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষ ও চলাচলের ফলে ঘটে, যা বায়ুমণ্ডলীয় পরিবর্তনের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয় না।
তবে কিছু পরোক্ষ সম্পর্ক বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন। যেমন মেরু ও পর্বতাঞ্চলে হিমবাহ গলে যাওয়ার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের ওপর চাপ হ্রাস পায়, যা টেকটোনিক ভারসাম্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং এর ফলে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তা বাড়তে পারে। আবার, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত বা বৃহৎ জলাধারে পানি জমার কারণে মাটির নিচে চাপ বাড়তে পারে, যা কিছু অঞ্চলে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা বাড়ায়।
সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য মানুষ দায়ী নয়—এই সত্যটি অনেক সময় আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিছু দুর্যোগ রয়েছে, যেগুলোর ফলে মানুষ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু এসব দুর্যোগ সৃষ্টির পেছনে মানুষের কোনো সরাসরি ভূমিকা নেই। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এটি মূলত ভূগর্ভস্থ ম্যাগমার অতিরিক্ত চাপের ফলে ঘটে এবং হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়ে বিস্তীর্ণ এলাকা ধ্বংস করে দিতে পারে।
তেমনি সুনামিও সাধারণত সমুদ্রের নিচে শক্তিশালী ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্টি হয় এবং উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাণঘাতী ঢেউ আছড়ে পড়ে। ভূমিকম্প নিজেও একটি স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক ঘটনা, যা টেকটোনিক প্লেটের চলাচলের ফলে সংঘটিত হয় এবং এতে মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই।
ঘূর্ণিঝড় কিংবা টর্নেডোও বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও তাপমাত্রার তারতম্যের ফলে সৃষ্টি হয়, যা প্রকৃতির নিজস্ব প্রক্রিয়া। পাহাড়ি এলাকায় ভূমি ভারসাম্য হারিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভূমিধস বা ভূস্খলনের ঘটনাও ঘটে, বিশেষ করে অতিবৃষ্টির সময়। এসব দুর্যোগের ভয়াবহতা উপেক্ষা করা যায় না, তবে এগুলোর জন্মে মানুষের ভূমিকা নেই, মানুষ বরং এসব দুর্যোগের নিরপরাধ শিকার।
২০০৮ সালের চীনের সিচুয়ান ভূমিকম্পের সম্ভাব্য একটি কারণ হিসেবে বৃহৎ জলাধারের পানির চাপকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব কারণেই বিজ্ঞানীরা মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তন ভূমিকম্প সরাসরি ঘটায় না, তবে এটি পরোক্ষভাবে কিছু ভৌগোলিক অঞ্চলে ভূমিকম্পের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।
আসলে জলবায়ু পরিবর্তন ও মানব দায়ের বিষয়টি এত বেশি আলোচিত হয়েছে যে বৃহত্তর জনমানসে একটি একমুখী ধারণা তৈরি হয়েছে। আমরা হয়তো অনেকেই জানি না যে, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ঘূর্ণিঝড় কিংবা ভূস্খলন—যেগুলো মানব সমাজে ভয়াবহ দুর্যোগ সৃষ্টি করে—এসব প্রকৃতির দৃষ্টিতে একটি ভৌগোলিক প্রয়োজন।
পৃথিবীর অভ্যন্তরে জমে থাকা প্রচণ্ড তাপ ও শক্তি নিঃসরণের জন্য ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি হলো প্রাকৃতিক নির্গমন প্রক্রিয়া। এসব না হলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে অস্থিতিশীলতা আরও বেড়ে যেত। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নতুন দ্বীপ ও ভূমি তৈরি হয়, সৃষ্টি হয় উর্বর মাটি, যা পরবর্তী সময়ে জীববৈচিত্র্যে সহায়ক ভূমিকা রাখে।
ঘূর্ণিঝড় বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় রাখে এবং বৃষ্টিপাতে সহায়তা করে। ভূস্খলনের মাধ্যমে পাহাড়ি এলাকার ভূ-আকৃতি স্বাভাবিকভাবে রূপান্তরিত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে নতুন নদী ও উপত্যকার জন্ম হয়। এসব প্রাকৃতিক ঘটনা মানব সমাজের জন্য ক্ষতিকর হলেও, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতি এগুলোর মাধ্যমে পৃথিবীকে ধারাবাহিকভাবে গঠন ও পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করে। তাই এসব দুর্যোগ প্রকৃতির জৈবিক চক্রের অংশ এবং পৃথিবীর ভৌগোলিক প্রয়োজন পূরণে অপরিহার্য।
তবুও মানুষ তার দায়িত্ব এড়াতে পারে না। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে হয়তো মানুষ থামাতে পারে না, কিন্তু এর ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য মানুষকেই দায়িত্ব নিতে হবে। এক্ষেত্রে সচেতন নগরায়ণ, দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রস্তুতি এবং পরিবেশবান্ধব পরিকল্পনা অপরিহার্য।
অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ বিপজ্জনক পাহাড়ি ঢালে বসতি গড়ে তোলে কিংবা নদীর ভাঙনপ্রবণ এলাকায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করে, যার ফলে ভূমিধস বা বন্যার ক্ষয়ক্ষতি বেড়ে যায়। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জলাধার ও জলাভূমি ভরাট এবং অপ্রতুল ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে ঘূর্ণিঝড় বা অতিবৃষ্টির সময় শহরগুলো জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে।
অন্যদিকে, পরিকল্পিত কৃষিকাজে বাঁধ, খাল ও জলাধার থাকলে অতিবৃষ্টি বা খরার সময় পানি সংরক্ষণ সম্ভব হয়, যা ফসল রক্ষায় সহায়ক। ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় ভূকম্পন-সহনশীল ভবন নির্মাণ, উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বন সংরক্ষণ, দুর্যোগ সতর্কবার্তা দ্রুত সম্প্রচার এবং উদ্ধার সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা—এসবই মানুষের করণীয়।
তাই বলা যায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়তো রোধ করা সম্ভব নয়, কিন্তু যথাযথ সচেতনতা ও পরিবেশবান্ধব নীতি গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ এর ভয়াবহতা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যথাযথ প্রস্তুতি ও সচেতনতা থাকলে বহু প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব।
ড. এ কে এম মাহমুদুল হক : অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ডিএম /সীমা


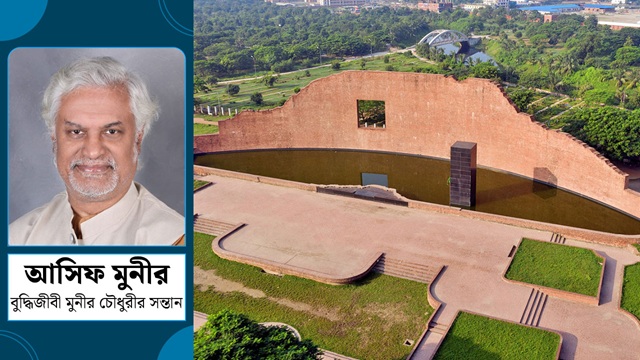

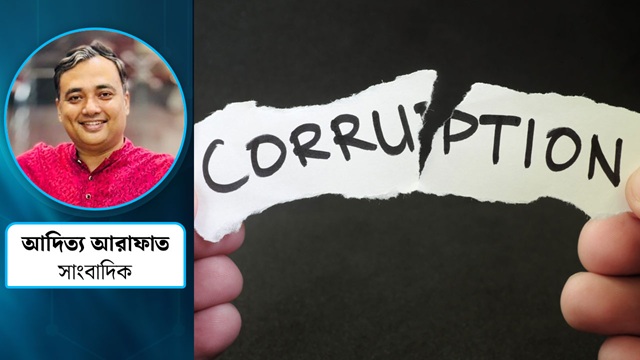



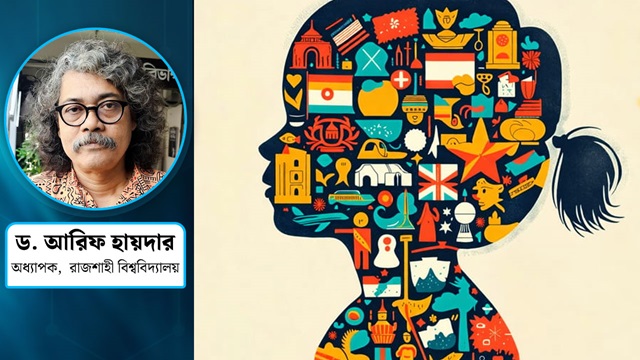
আপনার মূল্যবান মতামত দিন: